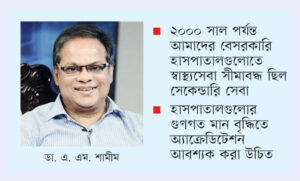মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণির বেশির ভাগই এখন দেশে চিকিৎসা নেয়। হৃদরোগ, কিডনি ইত্যাদির চিকিৎসা, কিংবা বিভিন্ন সার্জারি এখন দেশেই হচ্ছে (ডা. এ. এম. শামীম)
আশির দশকে বাংলাদেশের একজন মানুষ অসুস্থ হলে তার যথাযথ রোগ নির্ণয় সম্ভব হতো না। হাজার হাজার মানুষ ভারতে যেত। উচ্চবিত্তরা যেত সিঙ্গাপুরে। ওই সময় বাংলাদেশে ল্যাবএইড, পপুলার, ইবনে সিনাসহ আরো কয়েকটি আন্তর্জাতিক মানের রোগ নির্ণয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়।
একই ছাদের নিচে ভালো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, রোগ নির্ণয়ের আধুনিক সরঞ্জাম, ফার্মেসি—এই মডেলটি উপমহাদেশে প্রথম বাংলাদেশেই প্রতিষ্ঠা পায়। আজ পৃথিবীর যেখানেই যাওয়া হোক, স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্রগুলোতে এই মডেলটি দেখা যায়। বাংলাদেশের মফস্বল শহরগুলোতেও এখন ভালো রোগ নির্ণয় কেন্দ্র, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের উপস্থিতি—এই মডেলটি সফলভাবে কাজ করছে।
বাংলাদেশের ভালো রোগ নির্ণয় কেন্দ্র থেকে করা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল উন্নত বিশ্বের ভালো হাসপাতালগুলোতে গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে। ২০০০ সাল পর্যন্ত আমাদের দেশের বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে স্বাস্থ্যসেবা সীমাবদ্ধ ছিল সেকেন্ডারি সেবা, যেমন—সন্তান প্রসব, গলব্লাডার সার্জারি কিংবা সড়ক দুর্ঘটনায় চিকিৎসা—এতটুকুতেই। কিন্তু ২০০০ সালের পরে দেশে বেশ কিছু উন্নতমানের হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়। যেখানে পূর্ণকালীন ডাক্তার, নিজস্ব সিএসএসডি, কিচেন, লন্ড্রি, করপোরেট ব্যবস্থাপনাসহ আধুনিক বিশ্বের হাসপাতালগুলোর সমপর্যায়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকে। বর্তমানে বিশেষায়িত চিকিৎসার জন্য আমাদের দেশের বেশির ভাগ মানুষই দেশের এই নতুন প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালগুলোর ওপর নির্ভর করে, যেগুলো আস্থা ও বিশ্বাসযোগ্যতায় আগের চেয়ে অনেক এগিয়েছে।
আমাদের দেশে প্রায় ১০ হাজার প্রতিষ্ঠিত হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার আছে। এর মধ্যে গুণগত মানসম্পন্ন হাসপাতালের সংখ্যা এক হাজারের বেশি হবে না। উন্নতমান ও বিশ্বমানের কথা এলে প্রথমেই আসে হাসপাতালগুলোর ভৌতিক অবকাঠামো, প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি; পাশাপাশি সাপোর্ট সার্ভিস। ২০ বছর ধরে বেশ কিছু হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে। উন্নত বিশ্বের হাসপাতালের মতো। বলা যায়, ভৌত কাঠামো, প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির ব্যাপারে তুলনা করলে বাংলাদেশের বেশ কিছু হাসপাতালই আন্তর্জাতিক মানের। হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স, টেকনোলজিস্ট, স্বাস্থ্যকর্মী—সর্বোপরি একটি যথাযোগ্য ব্যবস্থাপনা একটি হাসপাতালকে রোগীর সেবা দেওয়ার উপযোগী করে তোলে।
বর্তমানে বাংলাদেশে ল্যাবএইডসহ বেশ কিছু হাসপাতালে পূর্ণকালীন ডাক্তার, মেডিক্যাল অফিসার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছে। হাসপাতালগুলো তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও নতুন নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে তাদের জ্ঞানকে সময়োপযোগী করে রাখে। এ ছাড়া ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের বাইরে থেকে প্রশিক্ষণ করিয়ে আনা, দেশে প্রশিক্ষক নিয়ে আসা হয়। বিদেশি বেশ কয়েকজন ডাক্তার, নার্স ও টেকনোলজিস্ট অনেক হাসপাতালে কাজ করছেন। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও একটি যথাযথ অর্গানোগ্রাম, স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ইথিক্যাল কমিটি, অডিট কমিটি, সাপ্লাই চেইন, সমন্বিত আইটি সিস্টেম ইত্যাদিসহ উন্নত বিশ্বের হাসপাতালগুলো যেভাবে চালিত হয়, তা দেশের বেশ কয়েকটি হাসপাতালে বিদ্যমান।
হাসপাতালের মান পরিমাপের জন্য বর্তমানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কতগুলো অ্যাক্রেডিটেশন বডি রয়েছে। যেমন—রোগ নির্ণয় কেন্দ্রের জন্য বাংলাদেশ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ‘বিএবি’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। একইভাবে আছে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ‘সিএপি’। হাসপাতালের মান নির্ণয়ের জন্য এই উপমহাদেশে রয়েছে ‘এনএবিএইচ’ নামের একটি প্রতিষ্ঠান। সারা বিশ্বের জন্য কাজ করছে ‘জেসিআই’ নামের প্রতিষ্ঠানটি। প্রতিষ্ঠানগুলো বাইরে থেকে তাদের দক্ষ অডিটর পাঠিয়ে হাসপাতালের খুঁটিনাটি বিষয়, যেমন—ভর্তি রোগী ও ডাক্তারের অনুপাত, নার্সদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে কোনো অপারেশন চলাকালীন কয়টি মপ রোগীর শরীরে ব্যবহার করা হলো এবং ব্যবহারের পর কয়টি ওয়েস্ট পেপার বক্সে এলো, তা গণনা করা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে থাকে।
৩০০ থেকে ৪০০ বিষয় পাঁচ-ছয়জন বিশেষজ্ঞ দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সরেজমিনে হাসপাতালে উপস্থিত থেকে পরিদর্শনের পর একটি কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট পাঠানো হয় এনএবিএইচের কেন্দ্রীয় অফিসে। পরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে এই ৩০০ থেকে ৪০০ বিষয়ের কোনোটিতে ঘাটতি থাকলে তার বিশদ বর্ণনা ও প্রতিকার সম্পর্কে রিপোর্ট পাঠানো হয়। পরবর্তী পর্যায়ে দক্ষ প্রশিক্ষকের মাধ্যমে ঘাটতির জায়গাগুলোতে উন্নতি সাধনের মাধ্যমে আবারও পরিদর্শন করে। এভাবে ত্রুটিমুক্ত হওয়ার পরে এনএবিএইচ বা জেসিআই কোনো হাসপাতালকে দুই বছরের জন্য অ্যাক্রেডিটেশন সার্টিফিকেট প্রদান করে। দুই বছর পরে আবারও একইভাবে অডিট করে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত অবস্থায় এনে সার্টিফিকেট নবায়ন করা হয়। আনন্দের বিষয়, ল্যাবএইড ডায়াগনস্টিক সেন্টার বাংলাদেশের প্রথম অ্যাক্রেডিটেশন বডির সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। একইভাবে ল্যাবএইডের দুটি হাসপাতাল বাংলাদেশে এনএবিএইচের অ্যাক্রেডিটেশনপ্রাপ্ত প্রথম হাসপাতাল।
বাংলাদেশের হাসপাতালগুলোর গুণগত মান বৃদ্ধি ও সংহত করার জন্য অ্যাক্রেডিটেশন আবশ্যক করে দেওয়া উচিত। এবার খরচের ব্যাপারে আলোকপাত করা যাক। বর্তমানে বাংলাদেশে ভালো হাসপাতালগুলোর রোগ নির্ণয় বাবদ যে খরচ রোগীর ওপর বর্তায়, তা ভারতের ভালো ভালো হাসপাতাল, যেমন—অ্যাপোলো, ফোর্টিস, মেদান্তা হাসপাতালের তিন ভাগের দুই ভাগ, ব্যাঙ্ককের বামরুনগ্রাদ, ব্যাঙ্কক জেনারেল হাসপাতালের চার ভাগের এক ভাগ, আর সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ, রাফেলস হাসপাতালের আট ভাগের এক ভাগ। বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে সেবা নিতে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের জন্য স্বাস্থ্য বীমা জরুরি হয়ে পড়েছে। কারণ সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে স্বাস্থ্য সমস্যার জন্য কোনো বাজেট থাকে না। সব শেষে আমরা আসি বাংলাদেশের বেসরকারি হাসপাতালগুলোর ব্যবস্থাপনার ওপর সাধারণ মানুষের আস্থার বিষয়ে। ২০০০ সালের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে এই আস্থা অনেকটাই বেড়েছে। মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণির বেশির ভাগই এখন দেশে চিকিৎসা নেয়। হৃদরোগ, কিডনি ইত্যাদির চিকিৎসা, কিংবা বিভিন্ন সার্জারি এখন দেশেই হচ্ছে। আর কভিডকালীন দুই বছর এ দেশের মানুষ সব পর্যায়ের চিকিৎসা দেশেই নিয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে হাসপাতালগুলোকে আরো জনমুখী হওয়া দরকার, বিশেষ করে ডাক্তারদের রোগীদের আরো বেশি সময় দেওয়া, নার্সদের আরো বেশি সহানুভূতিশীল হওয়া, টেকনোলজিস্টদের আরো দক্ষ হওয়া। এগুলো আমাদের কর্তব্য বলে মনে করি। তবেই বেসরকারি হাসপাতালের প্রতি সব মানুষের আস্থা আরো বাড়বে।
গত তিন দশকে বাংলাদেশ বেসরকারি পর্যায়ে অনেক এগিয়েছে। তার পরও সাধারণ মানুষ, গণমাধ্যমকর্মী, রেগুলেটরি সংস্থা, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ—সবাই মিলে একসঙ্গে জনমুখী পদক্ষেপ নিলেই শুধু এই আন্তর্জাতিক মানের হাসপাতালগুলো মানুষের হৃদয়ের আরো কাছে এসে সেবা দিতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।